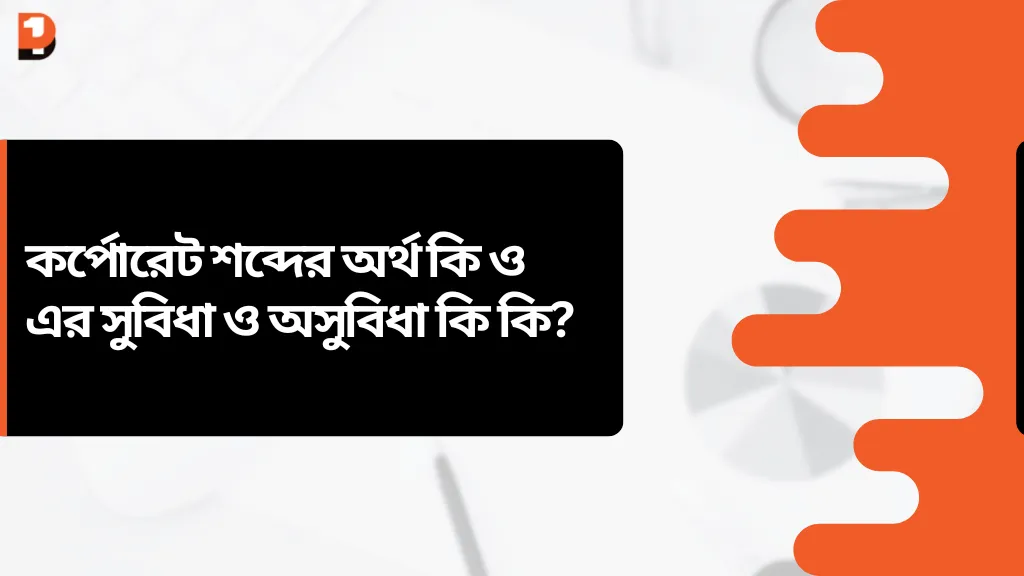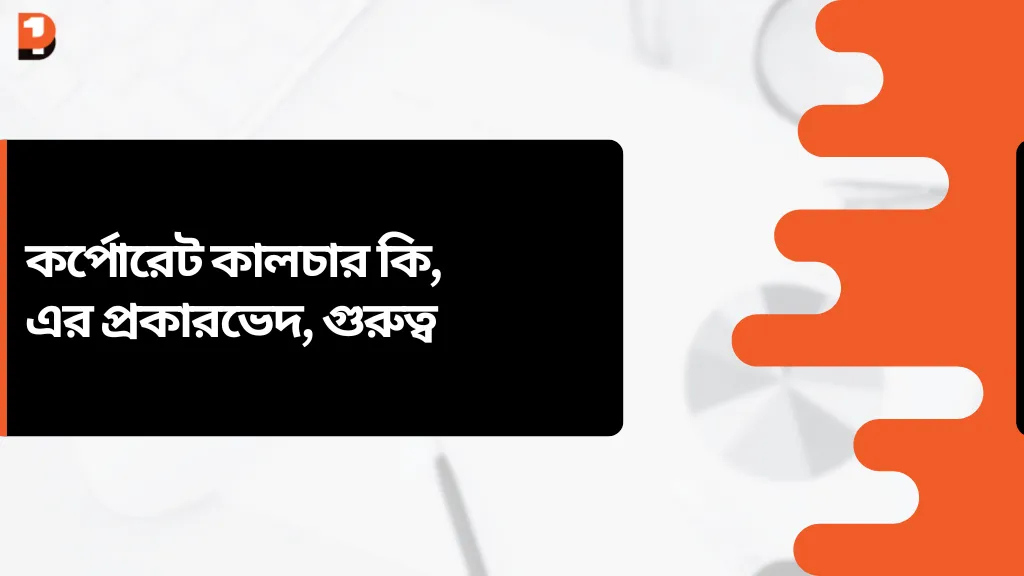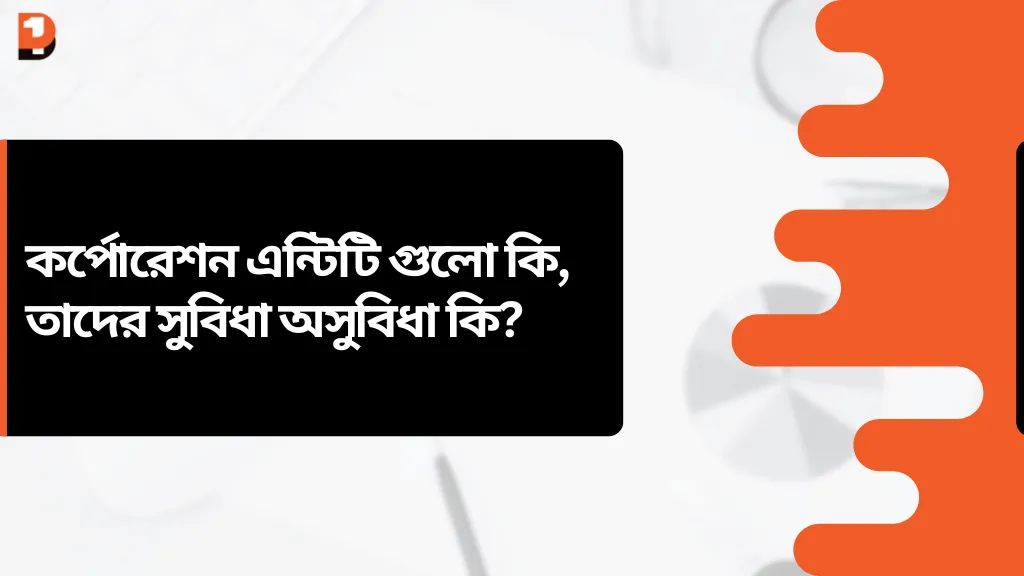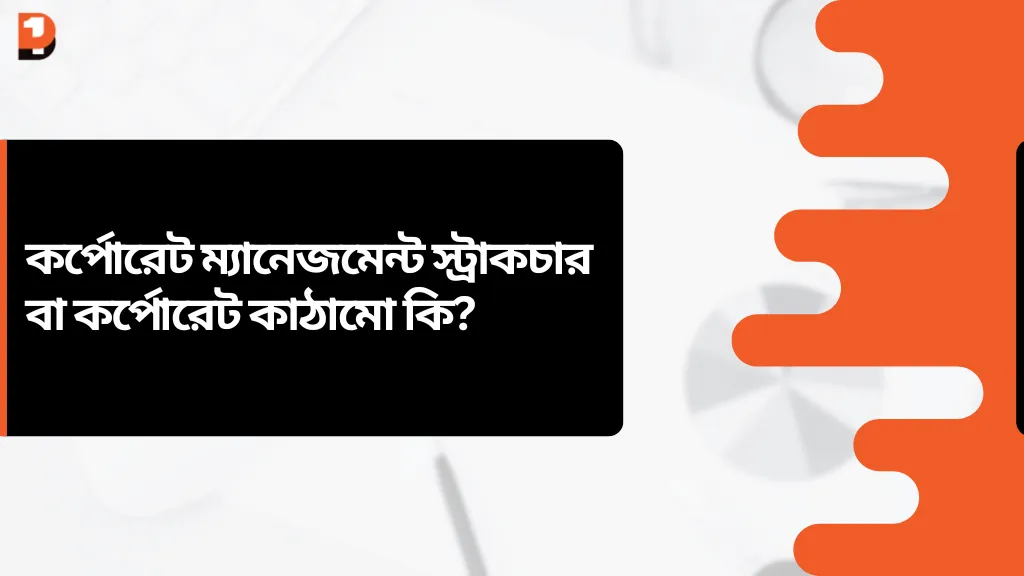এটি হচ্ছে এমন একটি বিষয় যেখানে কোম্পানির ভিতরে কীভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় তা নির্ধারণ করা হয়। জনপ্রিয় কর্পোরেট স্টাকচার মডেলের মধ্যে ফাংশনাল, ডিভিশনাল, ম্যাট্রিক্স, সার্কুলার ও ফ্লাট অন্যতম। এখানে পর্যায়ক্রমে সকল ধরনের কর্পোরেট এন্টিটিতে ও কোম্পানিতে কি স্ট্রাকচার অনুসরণ করা হয় তা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।
ফাংশনাল স্ট্রাকচার
কর্পোরেট মডেলগুলোর মধ্যে ফাংশনাল মডেল সব থেকে বেশি জনপ্রিয়। মাঝারী থেকে বড় কর্পোরেট গুলোর জন্য এই মডেল সব থেকে বেশি উপযুক্ত। এই মডেলে একই ধরনের স্কিল থাকা লোক দের নিয়ে গ্রুপ তৈরি করা হয়। অর্থাৎ এখানে স্কিলের উপর ভিত্তি করে ম্যানেজমেন্ট স্ত্রাকচার তৈরি করা হয়। উদাহরন স্বরূপ বলা যায় একটি কর্পোরেশনে যদি R&D ডিপার্টমেন্ট থাকে তাহলে এইখানে রিসার্চ, ডেভেলপমেন্ট ও টেস্টিং সম্পর্কিত কাজ হয়। অন্যদিকে একই প্রতিষ্ঠানের মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে শুধু সেলস ও কাস্টমার সাপোর্ট সম্পর্কে কাজ হয়।
সুবিধা
- প্রোডাক্টিভিটি: যে কর্পোরেশনে ফাংশনাল মডেল অ্যাপ্লাই করা হয় সেখানে প্রোডাক্টিভিটি অনেক বৃদ্ধি পায়। কারণ যখন একই স্কিলের কয়েকজন লোক একই বিষয়ে কাজ করে তখন সেখান থেকে ফলাফল অনেক দ্রুত আসে।
- স্কিল ডেভেলপমেন্ট: এই মডেলে সুপিরিয়র তার অর্জিত জ্ঞান তার আন্ডারে কাজ করা সবার সাথে শেয়ার করার সুযোগ পায়। এতে দেখা যায় যে এমপ্লয়ী খুব দ্রুত এবং সহজেই ইন্ডাস্ট্রি গ্রেড স্কিল শিখতে পারছে।
- ম্যানেজমেন্ট খরচ কমানো: গ্রুপ আকারে ডিপার্টমেন্ট ভাগ করার কারণে আলাদাভাবে কোন এমপ্লয়িকে ম্যানেজ করতে হচ্ছে না। পাশাপাশি ডিপার্টমেন্ট হেড বা ম্যানেজারকে দিয়ে সহজেই পুরো গ্রুপ পরিচালনা করা যাচ্ছে। এতে অতিরিক্ত খরচ করার প্রয়োজন পরছে না। যা প্রতিষ্ঠানের কস্ট কাটিং এ অনেক সাহায্য করে।
- জবাবদিহিতা এবং নিয়ন্ত্রণ: এই মডেলে গ্রুপের সকল কর্মীর কাজের হিসেব বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব থাকে ম্যানেজারের কাছে। ফলে বোর্ড অফ গভরনেন্স প্রতিটি ডিপার্টমেন্টের পারফর্মেন্স ও কার্যকারিতা অল্প সময়ের মধ্যে তদারকি করতে পারে। এতে ম্যানেজারদের যেমন দ্বায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায় তেমনি প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের উপর শক্ত নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখা সম্ভব হয়।
অসুবিধা
- ডিপার্টমেন্টাল প্রতিযোগিতা: ফাংশনাল মডেলে কোম্পানির প্রতিটি ডিপার্টমেন্ট ম্যানেজার দ্বারা ভাগ করা থাকে। প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে নির্দিষ্ট স্কিলের ইমপ্লয়ি থাকে। এতে তাদের যে ধরনের কাজ দেওয়া হয় তা অনেক দ্রুত সময়ে শেষ হওয়ার প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এতে দেখে যায় অনেক সময় ডিপার্টমেন্টাল প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়।
- সিদ্ধান্ত গ্রহনে ধিরতা: এই মডেলে ডিপার্টমেন্ট ম্যানেজার সরাসরি কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। তার টিম যদি নতুন কোন আইডিয়া নিয়ে আসে অথবা কাজ করার সময় যদি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন পরে তাহলে সরাসরি অ্যাকশন নেওয়া যায় না। প্রথমে ম্যানেজারকে তার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সাথে কথা বলতে হয়। এই কারণে সিদ্ধান্ত নিতে অনেক সময় দেরি হয়ে যায়।
- লিমিটেড ফ্লেক্সিবিলিটি: এই মডেলে ফ্লেক্সিবিলিটি অনেক কম। মদ্ধম পর্যায়ের কোন কোম্পানি যখন বড় হওয়া শুরু করে তখন ফাংশনাল মডেলে ফ্লেক্সিবিলিটি কাজ করে না। পাশাপাশি কোন ডিপার্টমেন্ট রিলোকেট করতে গেলেও অনেক ঝামেলায় পরতে হয়।
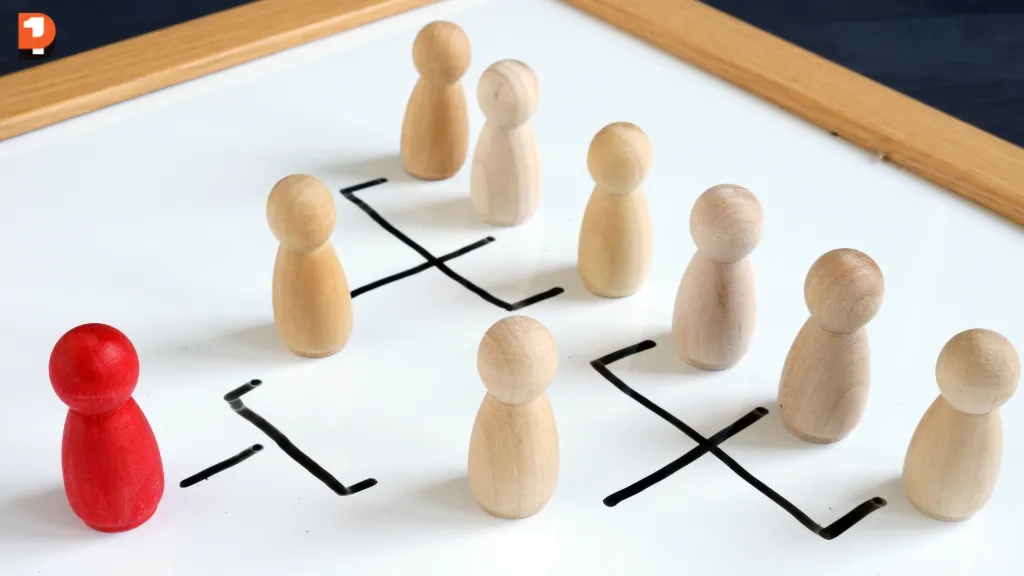
ডিভিশনাল স্ট্রাকচার
এই স্ট্রাকচারে বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া যেমন প্রোডাক্ট লাইন, ভৌগোলিক অবস্থান, মার্কেটের ধরণ ইত্যাদির ভিত্তিতে আলাদা আলদা বিভাগ তৈরি করা হয়। এখানে প্রতিটা বিভাগ স্বতন্ত্র বিজনেস হিসেবে নিজেদের কার্য সম্পাদন করে থাকে। যে কারণে তাদের ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে বাকি সব প্রশাসনিক কাজ স্বতন্ত্রভাবে হয়ে থাকে। তারা নিজেদের মধ্যে পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য তৈরি করে কাজ করে। যে কারণে এখানে ফ্লেক্সিবিলিটি থাকে এবং বৈশ্বিক কর্পোরেশন গুলোর জন্য এই স্ট্রাকচার অনেক বেশি কার্যকরী। তবে তারা আলাদা আলাদা ডিভিশন ভিত্তিক হিসেবে একটি প্রধান কর্পোরেশনের আওতায় থাকে।
সুবিধা
- ফোকাস স্পষ্ট থাকে: ডিভিশনাল স্ট্রাকচারে বিভাগ গুলো নির্দিষ্ট প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করতে পারে। অর্থাৎ তাদের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে একটি নির্দিষ্ট প্রোডাক্টকে গবেষণার মাধ্যমে গুণমান উন্নত করে বাজারজাত করা। যে কারণে উক্ত প্রোডাক্ট যে কাস্টমার গুলো ব্যবহার করে তারা সন্তুষ্ট থাকে।
- দ্বায়বদ্ধতা: এই মডেলে বিভাগগুলোকে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে দেওয়া হয়। যে কারণে তাদের আয় এবং ব্যায় তাদের নিজেদের উপরে বর্তায়। যে কারণে বিভাগীয় প্রধান তার ডিপার্টমেন্টে কাজ ঠিকভাবে হচ্ছে কি না এবং প্রফিট আসছে কিনা সে সম্পর্কে সবসময় অবগত থাকে। এতে বিভাগীয় প্রধানের কাছে বাকি কর্মকর্তাগন আয় এবং ব্যায়ের হিসেব নিয়ে দ্বায়বদ্ধ থাকে। যা মূল কর্পোরেশনের জন্য প্রায় সময় প্রফিটেবল হয়ে থাকে।
- ফ্লেক্সিবিলিটি: ডিভিসনাল স্ট্রাকচারে নতুন প্রোডাক্ট অ্যাড করা থেকে শুরু করে বিজনেস এক্সপ্যান্ড করার পুরোপুরি স্বাধীনতা থাকে। অন্যদিকে প্যারেন্ট কর্পোরেশন নতুন নতুন ডিভিশন তৈরির দ্বারা কোন বিজনেস বেশি প্রফিট করছে সে সম্পর্কে এক্সপেরিমেন্ট করতে পারে।
অসুবিধা
- প্রতিযোগিতা: ডিভিশনাল স্ট্রাকচারে সব থেকে বেশি যে সমস্যা হয় তা হচ্ছে প্রতিযোগিতা। ডিভিশন গুলো তাদের মধ্যকার পারফর্মেন্স, রিসোর্স ও কাস্টমার নিয়ে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করে। যা পক্ষান্তরে পুরো কর্পোরেশনের বিজনেসের উপরে সরাসরি প্রভাব ফেলে। অতিরিক্ত প্রতিযোগিতা ডিভিশনগুলোর মধ্যে ফাটল তৈরি করে যা তাদের একে অপরকে সহযোগিতার পথে বাঁধা সৃষ্টি করে। এতে সব থেকে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয় প্যারেন্ট কোম্পানি।
- অপ্রয়োজনীয় সম্পদের ব্যবহার: এই স্ট্রাকচারে প্রতিটি ডিভিশন তাদের নিজস্ব পরিচালক পর্ষদ দ্বারা পরিচালিত হয়। এখন একটি প্রতিষ্ঠানে যদি প্রতিটি বিভাগে আলাদা আলাদা HR, মার্কেটিং ও আর্থিক দিক গুলো পরিচালনা করার জন্য আলাদা লোক রাখা হয় তাহলে কর্পোরেশনের সার্বিক পরিচালনা খরচ বেড়ে যায়।
- অবকাঠামো কন্ট্রোল করা কঠিন: এই ধরনের স্ট্রাকচারে ডিভিশন গুলো একই কর্পোরেটের আন্ডারে থেকেও স্বতন্ত্রভাবে কাজ করে। যে কারণে এখানে মূল প্রতিষ্ঠানের নিয়মের সাথে ডিভিশন গুলোকে একত্র করে পরিচালনা করা অনেক কঠিন হয়ে পরে। অন্যদিকে ডিভিশনগুলো তাদের নিজেদের প্রায়োরিটি দিয়ে শুধু মাত্র নিজেদের উন্নতির দিকে গুরুত্ব দেয় যা অনেক সময় প্যারেন্ট কোম্পানির মিশন এবং ভিশনের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে।
ম্যাট্রিক্স স্ট্রাকচার
এটি ফাংশনাল ও ডিভিশনাল দুই ধরনের স্ট্রাকচারের সমন্বিত রুপ। অর্থাৎ ম্যাট্রিক্স স্ট্রাকচারে কর্পোরেট গুলো তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে ফাংশনাল মডেলে। অন্যদিকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ডিভিশনাল মডেল ইউজ করে যা প্রোজেক্ট নির্ভর বা প্রোডাক্ট নির্ভর কাজ করতে সহায়তা করে থাকে।
সুবিধা
- ডিপার্টমেন্ট গুলোর মধ্যকার সহযোগিতা: এই মডেলে ডিপার্টমেন্টগুলো তাদের একে অপরের সাথে কোলাবোরেশনের মাধ্যমে কাজ করে। যেহেতু এখানে প্রোজেক্ট ভিত্তিক কাজ হয় সেহেতু কর্মীদের মাঝে কাজের ব্যপকতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়।
- সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার: ম্যাট্রিক্স মডেলে এমপ্লয়ি গুলো ফাংশনাল ডিপার্টমেন্ট সিস্টেম থাকলেও তাদের বিভিন্ন প্রোজেক্টে কাজ করতে হয়। এতে কর্মীদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়। যে কারণে নতুন কোন প্রোজেক্ট শুরু করতে আর নতুন করে কর্মী হায়ার করার প্রয়োজন পরে না। যা পরক্ষভাবে সম্পদের অপচয় রোধ করে।
- কর্মীদের দক্ষতা বেশি থাকে: এই মডেলে কর্মীদের বিভিন্ন প্রোজেক্টে কাজ করার প্রয়োজন পরে যে কারণে তাদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়। এক প্রোজেক্ট থেকে দক্ষ কর্মী অন্য প্রোজেক্টে সহজে হস্তান্তর করা যায় জন্য সম্পদের এবং মেধার সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হয়।
অসুবিধা
- ম্যানেজমেন্ট অনেক কঠিন: এই মডেলে কর্মীদের একই সাথে বিভিন্ন প্রোজেক্টে কাজ করার প্রয়োজন পরে। পাশাপাশি কাজের অগ্রগতি ও প্রোজেক্ট সম্পর্কিত রিপোর্ট করা অনেক জটিল হয়। যে কারণে এই মডেলে সিদ্ধান্ত নিতে অপেক্ষাকৃত বেশি সময়ের প্রয়োজন পরে।
- অগ্রাধিকার বৈষম্য: ম্যাট্রিক্স স্ট্রাকচারে একই কাজের জন্য কয়েকবার রিপোর্ট করতে হয়। পাশাপাশি আলাদা আলাদা প্রোজেক্ট ম্যানেজার থাকায় অনেক সময় একই কাজের জন্য আলাদা আলাদা ইন্সট্রাকশন আসতে পারে। এতে কোন বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে এবং কোন বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে না তা নিয়ে ঝামেলার সৃষ্টি হয়।
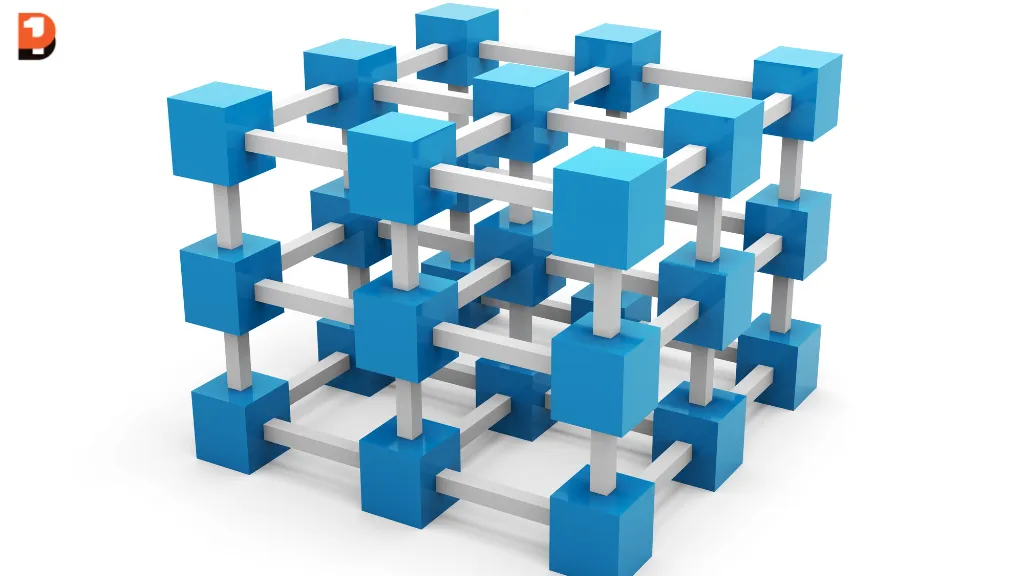
ফ্ল্যাট স্ট্রাকচার
ফ্লাট স্ট্রাকচারকে হরিজন্টাল স্ট্রাকচার হিসেবেও ডাকা হয়। এখানে সাধারণ কর্মী ও ম্যানেজমেন্টের মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষ থাকতে পারে আবার কিছু ক্ষেত্রে থাকে না। এই মডেলে ডিসিশন নেওয়ার বিষয় বিকেন্দ্রীকরণ হিসেবে থাকে। যে কারণে কোম্পানির স্বার্থে অনেক দ্রুত প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। এখানে একজন ম্যানেজার দ্বারা অনেক বড় আকারে কর্মী ম্যানেজ করা হয়। পাশাপাশি পদবীর উপরে ফোকাস না রেখে কাঁধে কাধ মিলিয়ে টিম ওয়ার্ক করাকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়।
সুবিধা
- স্বল্প খরচ: ফ্লাট মডেলে ম্যানেজমেন্টের খরচ খুব কম হয়। অন্যান্য মডেলে সাধারণ কর্মী থেকে পরিচালনা পর্ষদের মাঝে কয়েক লেয়ারের ম্যনেজমেন্ট থাকে। যা পুরো কর্পোরেটের ম্যানেজমেন্ট খরচ বৃদ্ধি করে দেয়। তবে ফ্লাট মডেলে সাধারণ কর্মী ও নির্বাহী পরিচালকের মাঝে সরাসরি যোগাযোগ করার সুযোগ থাকে।
- দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ: এই মডেলে মধ্যবর্তী ম্যানেজমেন্ট না থাকায় যে কোন সিদ্ধান্ত অনেক দ্রুত নেওয়া এবং প্রয়োগ করা সম্ভব হয়।
অসুবিধা
- পদোন্নতি সমস্যা: এই মডেলে সিইও ও সাধারণ কর্মীর মাঝে ম্যানেজমেন্টের জন্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ পদ থাকে না। এই কারণে উচ্চ পদে পদোন্নতি দেখা যায় না। এই কারণে অনেক কর্মী কাজের প্রতি আশানুরূপ ফোকাস রাখে না। যা মূল কর্পোরেশনের জন্য অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতির কারণ হয়ে দ্বারায়।
- ম্যানেজারের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হয়: ফ্ল্যাট স্ট্রাকচারে ম্যানেজারদের উপরে অনেক বেশি কাজের চাপ থাকে। কারণ একজন ম্যানেজারকে কমপক্ষে ১৫ থেকে ২০ জন কর্মীর দেখাশোনা করতে হয়।
সার্কুলার স্ট্রাকচার
সার্কুলার স্ট্রাকচারকে বলা হয় আধুনিক দুনিয়ার কর্পোরেট স্ট্রাকচার। এখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে শুরু করে পরিচালনার দায়িত্ব সার্কেলের উপরে থাকে। এই সার্কেল তৈরি হয় অভিজ্ঞদের দ্বারা। যারা একাধারে কয়েকটি বিষয়ে পারদর্শী থাকে। অন্যদিকে গতানুগতিক কর্পোরেট ম্যানেজমেন্ট ধারার পরিবর্তে এখানে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কাজ তাদের নিজেদের মধ্যেই বর্তায়। এখানে ডিপার্টমেন্ট সিস্টেম না তৈরি করে টিম, বা সার্কেল তৈরি করে কোম্পানি পরিচালনা করা হয়।
সুবিধা
- সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়: এই স্ট্রাকচারে সার্কেল গুলোর মধ্যে সমস্যা সমাধান, সৃজনশীল উদ্ভাবন ইত্যাদির মাধ্যমে কাজের গতি বৃদ্ধি পায়। টিম ওয়ার্ক করার কারণে কোন নতুন সমস্যার সমাধান অনেক দ্রুত করা সম্ভব হয়। যে কারণে বর্তমানে যে সকল কর্পোরেশন প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন নিয়ে কাজ করছে তারা এই স্ট্রাকচার ব্যাবহারের দিকে ঝুঁকে পরছে।
- দ্রুত সিদ্ধান্ত মেকিং: এই মডেলে ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে প্রোডাক্ট তৈরি, বিপণন সহ যাবতীয় কাজ সার্কেলে থাকা সবার মাঝে ভাগ করা থাকে। যে কারণে নতুন কোন সিদ্ধান্ত অনেক দ্রুত সময়ে নেওয়া সম্ভব হয়।
অসুবিধা
- নেতৃত্বের সংকট: যেহেতু এখানে গতানুগতিক কর্পোরেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম থাকে না সেহেতু নেতৃত্ব সংকট তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমন সার্কেল মডেলে পুরো সার্কেলটাকে কে নিয়ন্ত্রণ করবে তা নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।
- বড় কর্পোরেশনের জন্য প্রযোজ্য নয়: এই ধরনের মডেল বড় কর্পোরেশনগুলোর জন্য উপযুক্ত নয়। কারণ কর্পোরেশন যত বড় হয় তা সঠিক পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে তেমন শক্তিশালি ম্যানেজমেন্ট প্রয়োজন পরে।
শেষ কথা
কর্পোরেট স্ট্রাকচার মডেল প্রতিষ্ঠানের অন্তর্বর্তী কার্যক্রম কীভাবে পরিচালিত হয় তার ধারনা দেয়। অর্থাৎ কর্পোরেশন পরিচালনার জন্য ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে প্রোডাকশন লাইন কেমন হওয়া উচিত তা স্ট্রাকচার মডেল দ্বারা নির্ধারণ করা হয়। কোম্পানি পরিচালনার জন্য কোন স্ট্রাকচার মডেল উপযুক্ত তা এর এন্টিটি ও গঠনের উপরে নির্ভর করে।