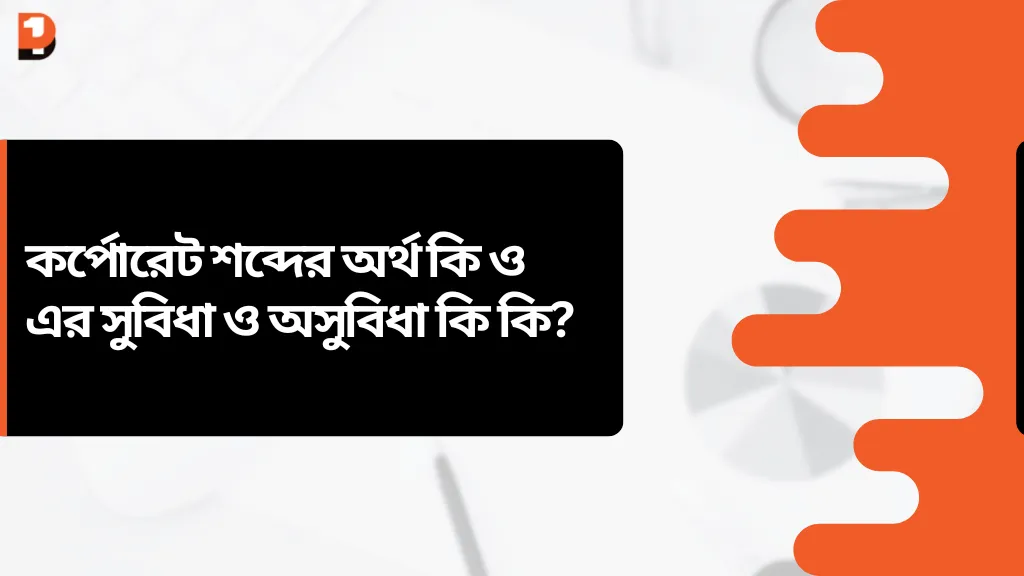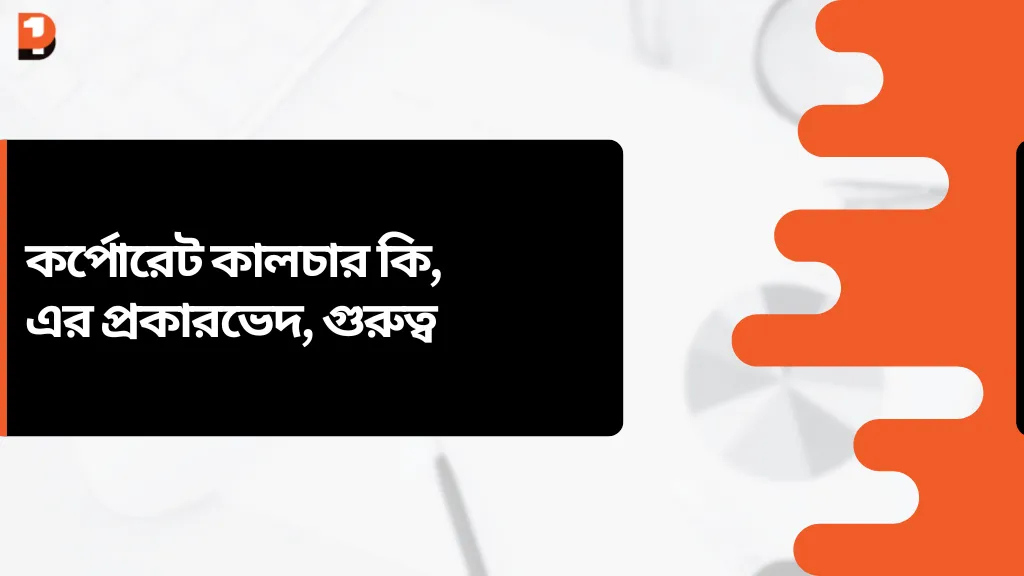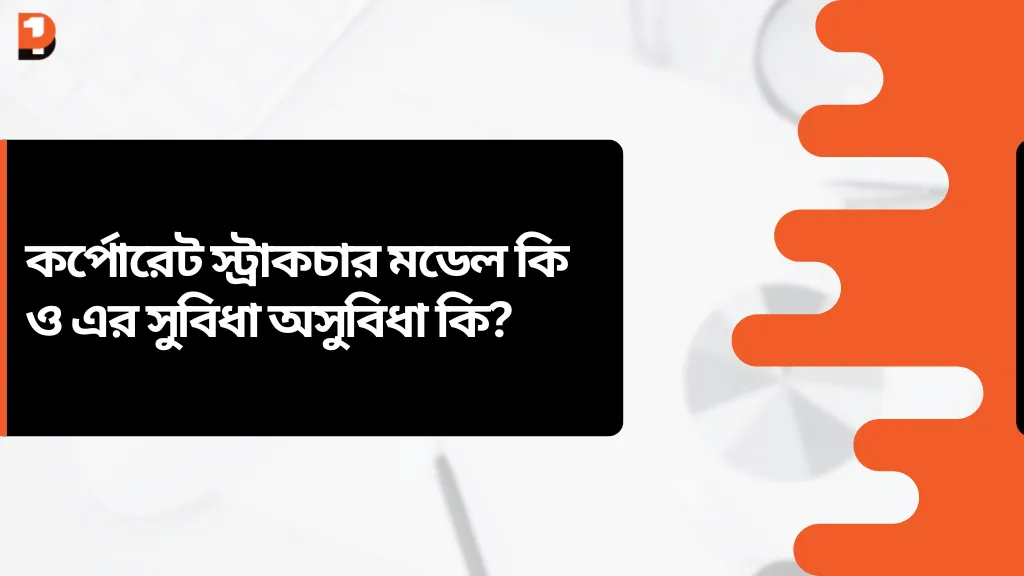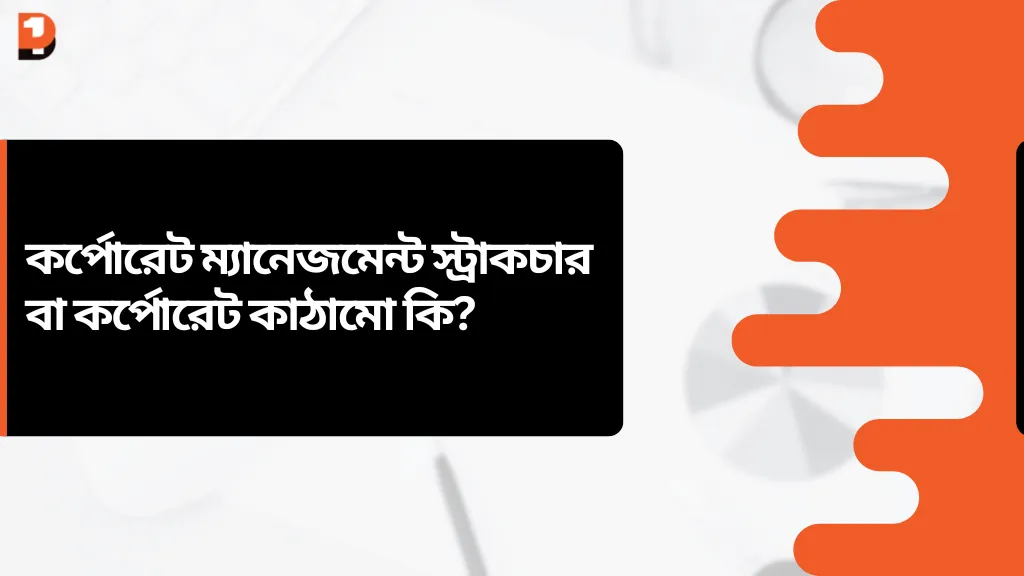কর্পোরেশন এন্টিটি হচ্ছে একটি কর্পোরেশনকে কত ভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যায় তার প্রকারভেদ। এটি দ্বারা কত ধরনের কর্পোরেশন হয় তা বোঝানো হয়ে থাকে। গঠনের উদ্দেশ্য ও শেয়ারের উপর ভিত্তি করে কর্পোরেশনকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। এখানে জনপ্রিয় কর্পোরেট এন্টিটি কি এবং এগুলোর সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।
পাবলিক কর্পোরেশন
পাবলিক কর্পোরেশন হচ্ছে ক্ষমতাসীন সরকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি। যা দেশের সংবিধান ও প্রচলিত আইন দ্বারা তৈরি ও পরিচালিত। মূলত পাবলিক কর্পোরেশন তৈরি করা হয় সরকার কর্তৃক। এই ধরনের প্রতিষ্ঠান তৈরি করার জন্য সংসদে আইন পাস করাতে হয়। পাবলিক কর্পোরেশন পরিচালনা করার জন্য আলাদাভাবে পরিচালনা পর্ষদ বা গভর্নিং বডি নিয়োগ দেওয়া হয়। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে সরকারের সরাসরি হস্তক্ষেপ থাকলেও মূল পরিচালনার দায়িত্ব থাকে পরিচালনা পর্ষদের কাছে।
আর্থিক দিক দিয়ে পাবলিক কর্পোরেশন স্বাধীন থাকে। অর্থাৎ শুরুর দিকে সরকার ফান্ডিং করলেও পরবর্তীতে পাবলিক কর্পোরেশনের গভর্নিং বডি কর্পোরেশন পরিচালনা করার জন্য অর্থ সংরক্ষণ ও নিজেদের বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে পারবে। পার্লামেন্টের আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও পাবলিক কর্পোরেশন স্বাধীন ও গণতান্ত্রিকভাবে কাজ করতে পারে। গভর্নিং বডি কোম্পানির উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় সকল ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। আমরা সকলেই জানি সরকারি প্রতিষ্ঠান গুলো অনেক ধীরগতিতে তাদের কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। যে কারণে মন্ত্রণালয় দ্বারা শুরু করা অনেক প্রোজেক্ট লম্বা সময় ধরে চলে।
এতে অপ্রয়োজনীয় অর্থ খরচ হওয়ার পাশাপাশি সময় নষ্ট হয়। এই দিক বিবেচনা করলে দেখা যাবে পাবলিক কর্পোরেশন স্বতন্ত্রভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং তা বাস্তবায়ন করতে পারে জন্য কাজের গতি বৃদ্ধি পায় ও দ্রুত সফলতা পাওয়া যায়। মূলত আজকের সিংগাপুর কিন্তু কয়েক দশক আগেই কিন্তু অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এত উন্নত ছিল না। তারা একটি ছোট বন্দরভিত্তিক রাষ্ট্র হয়ে দ্রুত উন্নতি করার পেছনে সব থেকে বড় কারণ হচ্ছে পাবলিক কর্পোরেশন। বাংলাদেশে এই রকম সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পাবলিক কর্পোরেশনের মধ্যে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (BPC) অন্যতম। প্রতিটি দেশের সরকার এই ধরনের কর্পোরেশন তৈরি করে থাকে। যা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে তবে মুনাফা সরকারের সাথে শেয়ার করে থাকে।

প্রাইভেট কর্পোরেশন
প্রাইভেট কর্পোরেশন হচ্ছে পাবলিক কর্পোরেশনের মতই এন্টিটি। তবে এই দুইটির মাঝে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে পাবলিক কর্পোরেশনের মালিকানা সরাসরি সরকারের কাছে থাকে। অন্যদিকে প্রাইভেট কর্পোরেশনের মালিকানা থাকে নির্দিষ্ট কোন কোম্পানি অথবা গোষ্ঠীর কাছে। পাবলিক কর্পোরেশনের শেয়ার স্টক মার্কেটে সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে। অন্যদিকে প্রাইভেট কর্পোরেশনের শেয়ার স্টক মার্কেটে লিস্ট করা হয় না।
পাবলিক কর্পোরেশনে অনেক ধরনের রুলস ও রেগুলেশন থাকে। কিন্তু প্রাইভেট কর্পোরেশনে অত বেশি রিকোয়ারমেন্ট থাকে না। এই ধরনের প্রতিষ্ঠান সাধারণত ছোট ইনভেস্টর গ্রুপ, ফ্যামিলি মেম্বার ও প্রাইভেট ফার্ম দ্বারা তৈরি ও পরিচালিত হয়। পাবলিক কর্পোরেশন থেকে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান ছোট হয় তবে কার্যকারিতার দিক দিয়ে এন্টারপ্রাইজ লেভেলের প্রোজেক্ট হ্যান্ডেল করতে পারে।
সুবিধা
- এখানে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব এবং অধিনস্ত পরিচালনা পদ্ধতি ও আর্থিক লেনদেন সম্পর্কে সকল তথ্য গোপন রাখা যায়। এতে সাধারণ জনগণ ও কম্পিটিটর থেকে নিজেদের সকল তথ্য ও দুর্বলতা গোপন রাখা যায়।
- এখানে নিয়মিতভাবে সরকারকে অথবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে রিপোর্ট করতে হয় না। পাবলিক রিভিউ না থাকায় অডিট রিপোর্ট, আর্থিক বিবৃতি ইত্যাদি তৈরি করার চাপ থাকে না এবং এই খাতে খরচ কমানো যায়।
- প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য দীর্ঘসূত্রিতা থাকে না। কারণ প্রাইভেট কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে মালিকানা গোষ্ঠী অনেক ছোট থাকে যা ডিসিশন মেকিং পদ্ধতিকে আরও গতিশীল করে তোলে।
- প্রাইভেট কর্পোরেশনে যারা শেয়ার হোল্ডার থাকে মূলত তারাই মূল কার্যক্রমে সরাসরি অংশগ্রহণ করে। যে কারণে প্রতিষ্ঠান তার গোল নিয়ে সমন্বিতভাবে দ্রুত এগিয়ে চলে ও সর্বোপরি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সফলের দিকে এগিয়ে চলে।
অসুবিধা
- পাবলিক কোম্পানির মূলধনের সাথে তুলনা করলে প্রাইভেট কোম্পানিতে মূলধন সংগ্রহ করা অনেক কঠিন হয়ে থাকে।
- এখানে প্রাইভেট কোম্পানি, ইনভেস্টর, লোন ইত্যাদির মাধ্যমে কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করার অর্থ সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।
- প্রাইভেট কর্পোরেশনের শেয়ার পরিবর্তন বা বিক্রি করা অনেক ঝামেলার হয়ে থাকে। এখানে শেয়ার বিক্রির আগে ইনভেস্টর ও অন্যান্য শেয়ার হোল্ডারদের সাথে বসে আলোচনার মাধ্যমে বিক্রির সিদ্ধান্ত নিতে হয়। যা প্রায় সময় মতের অমিল তৈরি করে থাকে।
সাবসিডিয়ারি কর্পোরেশন
সাবসিডিয়ারি কর্পোরেশন হচ্ছে অন্য কোন কর্পোরেশনের মালিকানায় থাকা কর্পোরেশন। অর্থাৎ যখন কোন কর্পোরেশন অন্য কোন কোম্পানি বা কর্পোরেশনকে কিনে নিবে তখন তা সাবসিডিয়ারি কর্পোরেশন হিসেবে পরিচালিত হবে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত অনেক কোম্পানি আছে যারা এই এন্টিটির মধ্যে পরে।
সাধারণত মূল কর্পোরেশন তাদের সাবসিডিয়ারি কোম্পানি গুলোর ৫০% বেশি শেয়ারের মালিক হয়ে থাকে। যদিও এই ধরনের প্রতিষ্ঠান নিজস্ব পরিচিতিতে চলে তবে প্রশাসনিক পরিচালনার দায়িত্ব থাকে প্যারেন্ট বা হোল্ডিং কর্পোরেশনের কাছে।
সুবিধা
- মূল প্রতিষ্ঠানের কাছে সকল ধরনের পরিচালনা ক্ষমতা থাকলেও সাবসিডিয়ারি আলাদা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত হয়।
- এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নিয়ম, পরিচালনা পদ্ধতি ও সম্পদ থাকে।
- কোন কর্পোরেশনের নিকট দায়বদ্ধ থাকলেও সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠানের আইনগত স্বাধীনতা থাকে। যে কারণে তাদের লোড বা পূর্বে থেকে থাকা কোন আইনগত জটিলতা প্যারেন্ট কোম্পানির উপর বর্তাবে না।
- বর্তমানে তিন ধরনের সাবসিডিয়ারি সিস্টেম রয়েছে যেখানে কোন কর্পোরেশন অন্য কোন কর্পোরেশনের ১০০%, ৫০% থেকে ১০০% অথবা ৫০% কম শেয়ারের মালিক হতে পারবে।
- এই ধরনের কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে দুইভাবে ট্যাক্স ফাইল করার যায়। প্রথমত সাবসিডিয়ারি আলাদাভাবে তার ট্যাক্স দিতে পারবে অন্যদিকে প্যারেন্ট কর্পোরেশন তার আন্ডারে থাকা সকল সাবসিডিয়ারির ট্যাক্স জমা দিতে পারবে।
অসুবিধা
- সাধারণত সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান গুলো প্যারেন্ট কর্পোরেশন যে দেশে সেই দেশে হওয়ার পাশাপাশি বাইরের দেশেও হতে পারে। এই ক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে আর্থিক ও অন্যান্য বিষয়ে জটিলতা তৈরি হয়।
- অন্যদিকে ভিন্ন দেশে থাকা কোন সাবসিডিয়ারির ট্যাক্স দেওয়ার সময় প্রায় ক্ষেত্রে সুবিধা পাওয়া যায়। তবে এতে ডাবল ট্যাক্স দেওয়ার মতো ঝামেলা তৈরি হতে পারে।
হোল্ডিং কর্পোরেশন
হোল্ডিং কর্পোরেশন নিজে কোন প্রোডাক্ট তৈরি করে না। বরং তারা তাদের আন্ডারে থাকা বিভিন্ন সাবসিডিয়ারি কোম্পানি গুলোর ইনভেস্টমেন্ট সহ সর্বোপরি ম্যানেজমেন্ট তদারকি করে থাকে। হোল্ডিং কর্পোরেশনের সব থেকে বড় উদাহরণ হচ্ছে Alphabet Inc. যাকে আমরা গুগলের প্যারেন্ট কোম্পানি হিসেবে চিনি। এই কর্পোরেশনের আন্ডারে আরও অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যারা স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের কাজ করে তবে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর শেয়ার ম্যানেজমেন্ট করার কাজ Alphabet নিজে করে থাকে।
সুবিধা
- এই ধরনের কর্পোরেশন সাধারণত অনেক কোম্পানির শেয়ার কিনে থাকে। যে কারণে তারা কোন প্রকারের প্রোডাক্ট তৈরি না করেই একই সাথে অনেক কোম্পানির মালিক হতে পারে।
- কোন কারণে কোন সাবসিডিয়ারি দেউলিয়া হয়ে গেলে, আইনগত ঝামেলায় পড়লে অথবা লসের সম্মুখীন হলে তা হোল্ডিং কর্পোরেশনের উপর বর্তায় না।
- হোল্ডিং কর্পোরেশন তার মালিকানাধীন কোন প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে না বরং বছর শেষে উন্নতি ও অবনতির হিসেব করে থাকে।
- হোল্ডিং কর্পোরেশনের আন্ডারে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি সাবসিডিয়ারি হিসেবে থাকতে পারে। যা ডাইভারসিটি তৈরি করে।
অসুবিধা
- একই সাথে অনেক গুলো সাবসিডিয়ারি কোম্পানি পরিচালনা করা অনেক কঠিন। সঠিকভাবে এই প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনা করার জন্য অনেক শক্তিশালী গভর্নেন্স বডির প্রয়োজন হয়।
- নিয়মিতভাবে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের তদারকি করা হয় না জন্য অনেক ধরনের পরিবর্তনের সাথে হোল্ডিং কর্পোরেশনের দূরত্ব তৈরি হয়। অন্যদিকে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সময় বেশি লাগে।
- হোল্ডিং কর্পোরেশনকে অনেক দেশের সরকার একচেটিয়া বিজনেসের সম্ভাবনা মনে করে অতিরিক্ত ট্যাক্স সহ অন্যান্য লিগ্যাল শর্ত আরোপ করতে পারে।

মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন
আমরা সবাই অবচেতন ভাবে মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন সম্পর্কে ধারণা রাখি। এই ধরনের প্রতিষ্ঠান সাধারণত নিজের দেশে সেন্ট্রাল অফিস রেখে বাইরে অন্য দেশে ব্রাঞ্চ তৈরি করে কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই ধরনের কর্পোরেশন অন্য দেশে প্রতিষ্ঠান খোলার পাশাপাশি পণ্য তৈরি ও বিক্রি করে থাকে। গ্লোবাল মার্কেটে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক উন্নতিতে সবথেকে বেশি প্রভাব বিস্তার করে।
সুবিধা
- মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন একের অধিক দেশে সাবসিডিয়ারি, ব্রাঞ্চ ও ভেঞ্চারের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। এতে একই সাথে কয়েকটি দেশের অর্থনীতিতে প্রবেশ করার সুযোগ হয়।
- একটি সেন্ট্রালাইজড হেডকোয়ার্টার থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় জন্য কাজের গতি অনেক বেশি থাকে এবং যে কোন সিদ্ধান্ত অনেক দ্রুত নেওয়া সম্ভব হয়। এতে সমস্যা সমাধান ও নতুন ইনোভেশন করা সহজ হয়।
- শক্তিশালী পরিচালনা পর্ষদ থাকায় এই ধরনের কর্পোরেশন অনেক বড় আকারে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। অন্য দেশের সরকারের সাথে সরাসরি কাজ করার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রোজেক্টে ইনভেস্ট করতে পারে।
অসুবিধা
- আলাদা আলাদা দেশে থাকার কারণে মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশনকে আলাদা আলাদা শ্রম আইন সহ অন্যান্য অবশ্য পালনীয় আইন অনুসরণ করতে হয়।
- লোকাল কাস্টমারদের রুচি ও পণ্য কেনার অভ্যাস ভালো করে ধারণা করতে না পারলে অনেক সময় আর্থিক লসের সম্মুখীন হতে হয়।
- বিভিন্ন ধরনের সমালোচনা সহ রাজনৈতিক সমস্যার কারণে অনেক সময় মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশনকে আর্থিক ক্ষতির মধ্যে পরতে হতে পারে।
নন-প্রফিট কর্পোরেশন
নামের মধ্যেই এই ধরনের কর্পোরেশনের বৈশিষ্ট্য লুকায়িত আছে। যেখানে অন্যান্য কর্পোরেশন তাদের শেয়ার হোল্ডার ও ফাউন্ডারদের লাভের জন্য কাজ করে সেখানে নন-প্রফিট কর্পোরেশন অনেকটা আলাদা। এই ধরনের প্রতিষ্ঠান গুলোর প্রধান উদ্দেশ্য থাকে বিভিন্ন সেবামূলক কাজ যেমন শিক্ষা, চিকিৎসা, সামাজিক জীবন ইত্যাদি সেক্টরে অবদান রাখা। তারা তাদের বিভিন্ন প্রোজেক্ট এবং ইনভেস্টরস থেকে আর্থিক সাহায্য নেয় এবং তা তাদের সেবামূলক বিভিন্ন প্রোজেক্টে ইনভেস্ট করে।
সুবিধা
- নন-প্রফিট কর্পোরেশন মহামারি থেকে শুরু করে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশগুলোয় সহায়তা করে থাকে।
- নিজেদের দেশের ভেতরে কোন প্রকারের সেবা মুলক কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজন পড়লে এই ধরনের কর্পোরেশন এগিয়ে আসে।
- নন-প্রফিট কর্পোরেশন পরিচালিত হয় ভলান্টিয়ার গভর্নিং বডি দ্বারা। যারা কর্পোরেশন থেকে কোন প্রকারের আর্থিক সুবিধা নেয় না।
- এই ধরনের কর্পোরেশনের জন্য বিভিন্ন দেশের সরকার ট্যাক্স মওকুফ করার সুবিধা দিয়ে থাকে। অর্থাৎ নন-প্রফিট কর্পোরেশনগুলো ট্যাক্স না দিয়েও লিগ্যালভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।
অসুবিধা
- নন-প্রফিট কর্পোরেশনের সব থেকে বড় সমস্যা হচ্ছে এটি বিভিন্ন সরকারের বা পলিটিক্যাল পার্টির সুবিধা ভোগ করার একটি পন্থা হিসেবে কাজ করতে পারে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে পলিটিক্যাল ইনভলভমেন্ট অনেক বেশি থাকে।
- এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের রেভিনিউ জেনারেট করার তেমন মাধ্যম থাকে না। আর তারা যা আয় করে তা আবার তাদের অন্য প্রোজেক্টে ব্যয় করে। এতে আর্থিক দিক দিয়ে সুবিধা পেতে তাদের ডোনেশন এর উপরে নির্ভর করতে হয়।
প্রফেশনাল কর্পোরেশন
এটি এমন একটি কর্পোরেশন যা সার্ভিস প্রদান করতে লাইসেন্স লাগে এমন প্রফেশনালদের দ্বারা তৈরি। অর্থাৎ লাইসেন্সপ্রাপ্ত ডাক্তার, উকিল, প্রকৌশলী, হিসাব রক্ষক ইত্যাদি পেশাজীবী দ্বারা তৈরি করা কর্পোরেশনকে প্রফেশনাল কর্পোরেশন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে তারা যেন সার্ভিস প্রদান করতে পারে। এটি অনেকটা সিন্ডিকেটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অন্যদিকে কর্পোরেশনের শেয়ারহোল্ডার একই প্রফেসনের বাইরের কেউ হতে পারবে না।
এতে একটা কমিউনিটি তৈরি হওয়ার পাশাপাশি নিজেরা আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হয়। অন্যদিকে যখন কেউ প্রফেশনাল ডিগ্রী অর্জন করে তখন সরকার থেকে লাইসেন্স পেতে প্রফেশনাল কর্পোরেশন সাহায্য করে। কারণ অনেক দেশে লাইসেন্স এর জন্য অ্যাপ্লাই করলে প্রফেশনাল কর্পোরেশন এর সদস্য কিনা তা জানতে চায়। প্রফেশনাল কর্পোরেশনের সদস্য হলে লাইসেন্স পাওয়া সহ নিজেদের বিভিন্ন দাবি সরকারের কাছে সহজে উপস্থাপন করা সহজ হয়।
সুবিধা
- প্রফেশনাল কর্পোরেশনের শেয়ার হোল্ডার দের মধ্যে একটি প্রফেসনালিজম প্রকাশ পায়।
- প্রফেশনালদের লিগালি প্রটেক্ট করার জন্য এই ধরনের কর্পোরেশন অনেক কাজে লাগে।
- এই ধরনের প্রতিষ্ঠান সাধারণত C-Corp হিসেবে ট্যাক্সের আওতায় পরে তবে কিছু কিছু জায়গায় ডাবল ট্যাক্স এড়ানোর জন্য S-Corp হিসেবেও ট্যাক্স প্রদান করে থাকে।
- অন্য লাইসেন্স ধারির কাছে শেয়ার বিক্রি করে দেওয়ার মাধ্যমে মালিকানা পরিবর্তন করা যায়।
- এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের শেয়ার অন্য কোন প্রফেশনের কেউ নিতে পারবে না। যে কারণে কোন ধরনের কনফ্লিক্ট তৈরি হয় না।
- কোম্পানির দেনা-পাওনা ও আইন বিষয়ক কোন সমস্যা থাকলে তা শেয়ার হোল্ডারদের উপর বর্তায় না।
অসুবিধা
- এই ধরনের প্রতিষ্ঠান C-Corp হিসেবে বিবেচনা করা হয় জন্য অনেক সময় ডাবল ট্যাক্স দেওয়ার ঝামেলায় পরতে হয়।
- অন্য ইন্ডাস্ট্রির কেউ এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কিনতে পারে না। অর্থাৎ যে প্রফেশনের দ্বারা উক্ত কর্পোরেশন তৈরি শেয়ার কিনতে গেলে ওই প্রফেশনের লাইসেন্স থাকতে হবে।
S-Corp কর্পোরেশন
এটি মূলত একটি বিশেষ ধরনের কর্পোরেশন এন্টিটি। এটি সাধারণত আমেরিকায় প্রচলিত রয়েছে। S-Corp ছোট ও মাঝারি গোত্রের বিজনেসের জন্য সব থেকে বেশি প্রযোজ্য। এর কারণ হচ্ছে কর্পোরেশনের জন্য সরকার অনেক বেশি পরিমাণে ট্যাক্স নির্ধারণ করে থাকে। কিন্তু S-Corp কর্পোরেশনের আন্ডারে ট্যাক্সের পরিমাণ অনেক কমে যায়।
সুবিধা
- অন্যান্য এন্টিটিতে ফুল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ট্যাক্স দিতে হয়। কিন্তু এখানে শুধু শেয়ারহোল্ডারের ইনকামের উপর ট্যাক্স দিতে হয়।
- ডাবল ট্যাক্স দেওয়ার সমস্যায় পরতে হয় না।
- অন্যান্য কর্পোরেশনের মতো এখানেও অ্যাসেটের প্রোটেকশন পাওয়া যায়।
- এখানে সকল শেয়ার হোল্ডারের সমান অধিকার থাকে এবং সবাই সিদ্ধান্ত দিতে পারে।
- স্যালারি বাদেও কর্পোরেশন যদি কোন প্রোজেক্ট থেকে বেশি ইনকাম করে তাহলে লাভের অংশ সবার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়।
অসুবিধা
- ছোট ও মাঝারি বিজনেসের জন্য প্রযোজ্য।
- ১০০ এর উপরে শেয়ারহোল্ডার নেওয়া যায় না।
- আমেরিকার সিটিজেন ছাড়া অন্য কেউ শেয়ার নিতে পারে না।
- ওয়ান ক্লাস অফ স্টক সিস্টেম থাকার কারণে বড় বড় ইনভেস্টর এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে ইনভেস্ট করতে আগ্রহ বোধ করে না।

C-Corp কর্পোরেশন
এটি হচ্ছে গতানুগতিক কর্পোরেশন এন্টিটি। এই স্ট্রাকচারে সবার উপরে থাকে শেয়ার হোল্ডারস যারা বোর্ড অফ ডিরেক্টর দিয়ে কর্পোরেশন পরিচালনা করে থাকে। পরবর্তীতে বোর্ড অফ ডিরেক্টরগন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য CEO, COO ইত্যাদি অফিসার নিয়োগ দেন। যারা পরবর্তীতে কর্মচারী দ্বারা কর্পোরেশনের উদ্দেশ্য পূরণে কাজ করে থাকে।
সুবিধা
- এখানে শেয়ারহোল্ডার রাখার নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা নেই। অর্থাৎ এখানে অগণিত পর্যায়ে শেয়ার বিক্রি করার সুযোগ থাকে। C-Corp এ ব্যক্তি থেকে শুরু করে প্রতিষ্ঠান ও অন্য এন্টিটি শেয়ার নিতে পারে।
- ইচ্ছা মতো শেয়ার তৈরি করা যায় জন্য ইনভেস্টরদের প্রায়োরিটি লিস্টে C-Corp সব থেকে উপরে থাকে। যে কারণে এই কর্পোরেশনে মূলধনের কমতি পরে না।
- C-Corp সহজেই পাবলিক কর্পোরেশন হিসেবে বহিঃপ্রকাশ করতে পারে। এতে বিনিয়োগ পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়।
- শেয়ার হোল্ডার বা মালিক বারবার পরিবর্তন হলেও কর্পোরেশন তার নিজ গতিতে চলতে থাকে।
অসুবিধা
- প্রায় সময় ডাবল ট্যাক্স দেওয়ার সমস্যায় পরতে হয়। অর্থাৎ C-Corp এ কোম্পানি ও এর শেয়ার হোল্ডারদের একত্রিত করা আয়ের উপরে ট্যাক্স দিতে হয়। পাশাপাশি এর শেয়ারহোল্ডার দের আলাদাভাবে তাদের নিজের ইনকামের উপরে ট্যাক্স দিতে হয়।
- অনেক কঠিন এবং অবশ্য পালনীয় রুলস ফলো করতে হয়। যা অনেক সময় অতিরিক্ত সময় নষ্ট করায়।
- ছোট ও মাঝারি বিজনেসের জন্য এই কর্পোরেশন এন্টিটি উপযুক্ত নয়।
B-Corp কর্পোরেশন
B-Corp কে বলা হয় বেনিফিট কর্পোরেশন। অর্থাৎ এই ধরনের কর্পোরেশনের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে বেনিফিট করা। গতানুগতিক কর্পোরেশনে শুধু শেয়ারহোল্ডার দের কথা চিন্তা করা হয়। কিন্তু B-Corp য়ে প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মচারী, ইনভেস্টর, সাপ্লায়ার, কাস্টমার, পরিবেশ ও লোকাল কমিউনিটির কথা চিন্তা করা হয়।
সুবিধা
- B-Corp কর্পোরেশনে লাভের কথা চিন্তা করার পাশাপাশি সমাজ ও পৃথিবীতে কি ইমপ্যাক্ট ফেলবে সে বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে থাকে।
- এই ধরনের কর্পোরেশনে সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নতির কথা চিন্তা করে কাজ করে।
- B-Corp যদি রেজিস্ট্রেশন করাতে হয় তাহলে B Lab থেকে অ্যাপ্রুভ করে নিতে হয়।
- এই ধরনের কর্পোরেশন পরিচালনা করা হয় একটি বোর্ড অফ গভর্নেন্স দ্বারা। তারা শেয়ার হোল্ডার দের উদ্দেশ্যকে মডিফাই করে কাজ করে। যাতে সামাজিক ও পরিবেশগত উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পাশাপাশি আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান হওয়া সম্ভব হয়।
অসুবিধা
- B-Corp এর মান অনেক উন্নত হতে হয় যা এর পরিচালনা খরচ অনেকগুণ বৃদ্ধি করে।
- আর্থসামাজিক দিকে ইনভেস্ট করে তেমন বেশি পরিমাণে আয় করা যায় না। যা শেয়ারহোল্ডার দের জন্য অসুবিধার হহে থাকে।
- ট্রান্সপারেন্সি থাকতে হয় এবং প্রতি বছর কি পরিমাণে আয় ব্যয় হয় তা অবশ্যই পাবলিকের সামনে প্রকাশ করতে হয়।
শেষ কথা
কর্পোরেট এন্টিটি দ্বারা উক্ত প্রতিষ্ঠান কি ধরনের, এখানে ইনভেস্ট করা যাবে কি যাবে না এবং শেয়ার কেনা উচিত হবে কি না এই সকল বিষয়ে ধারণা পাওয়া যায়। বিশ্বব্যাপি বেশ কয়েকটি কর্পোরেট এন্টিটি প্রচলিত রয়েছে। এখানে সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেওয়া হয়েছে।